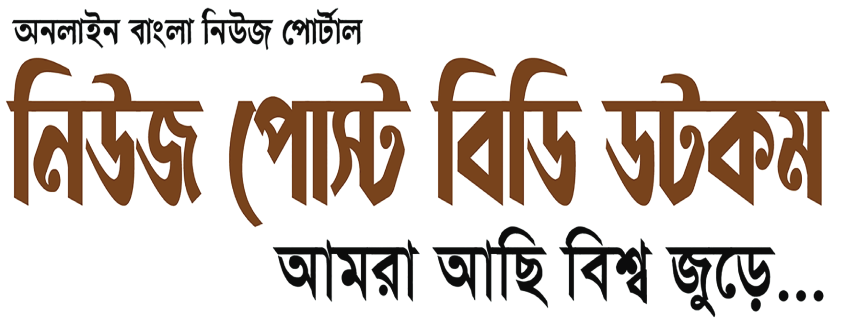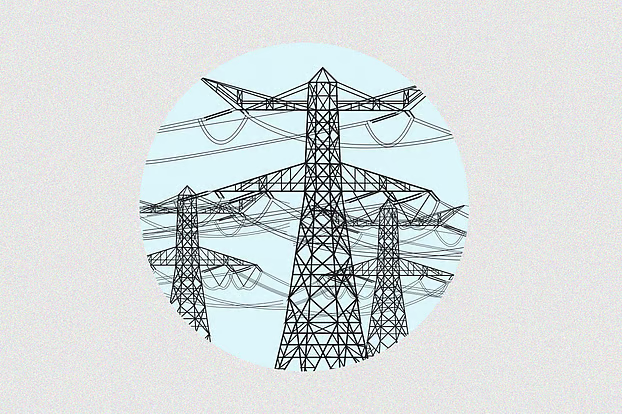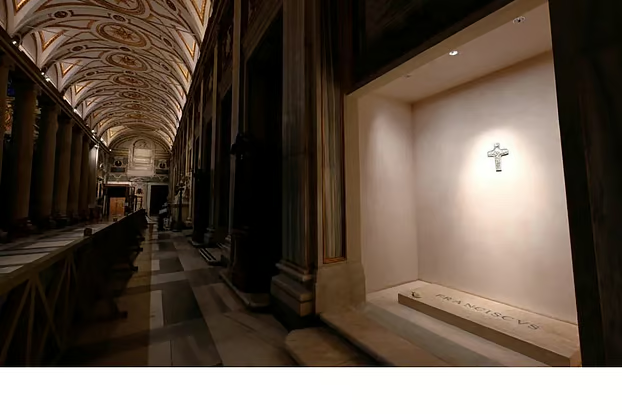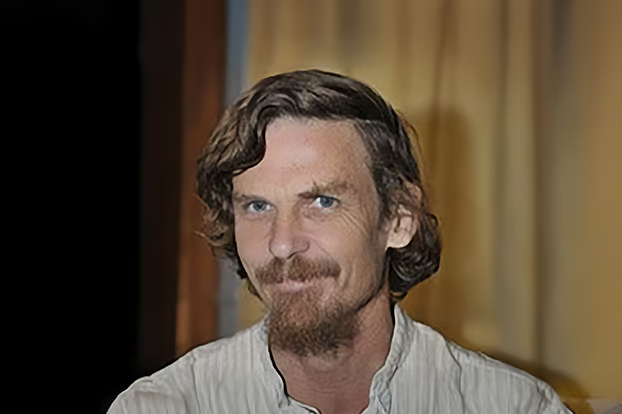
নিজেস্ব প্রতিবেদক:
আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে, নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে হাতে গোনা কয়জন অর্থনীতিবিদই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ভবিষ্যতে শিশুমৃত্যুর হার ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে কমবে। অথচ তখন ভারতের মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন শুধু বেশিই ছিল না, বরং বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ছিল দ্রুততর। এমনিতে ভারতে শিশুমৃত্যুর হার নিচের দিকেই থাকে, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে শুরু করলে প্রথম প্রথম ভাবা হতো, এই পার্থক্য ভারতের অনুকূলেই যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটল ঠিক উল্টোটা। বাস্তবে ভারতের উল্লম্ফন ঘটল বটে, তবে তা সামনে নয়, পেছনের দিকে।
শেষ পর্যন্ত দুই দশক আগে বিষয়টি যখন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল, প্রথমে তা একধরনের স্বল্পমেয়াদি অসংগতি বলে মনে করা হলো। কারণ, ভাবা হতো, ভারত মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনে উচ্চতর অবস্থানে থেকে ও উচ্চ গতির আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে এবং সামাজিক সুরক্ষায় বড় মাপের ব্যয় করে ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে আজ হোক কাল হোক, বাংলাদেশকে টপকে যাবে। কিন্তু হায়! ভাবলেই সেটি বাস্তব হয়ে যায় না। যা আশা করা হচ্ছিল, প্রকৃতপক্ষে তার বিপরীতই ঘটল। তথ্য–উপাত্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, মানব উন্নয়নের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশ ভারতকে অতিক্রম করেছে। এটি শুধু শিশুমৃত্যুর হারেই নয়, বরং সাধারণভাবে শিশু উন্নয়ন থেকে শুরু করে জন্মের সময় বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত আয়ু (প্রচলিত শব্দচয়নে গড় আয়ু), স্কুলশিক্ষায় অংশগ্রহণ, লিঙ্গসমতাসহ আরও অন্য সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের তুলনায় পেছনে পড়েছে লজ্জাজনকভাবে, যেমন স্যানিটারি বা পাকা পায়খানার ব্যবহার যার বড় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে ২০১১ সালের মধ্যেই উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ কার্যত শূন্যে চলে আসে, যদিও ভারতে তা ব্যাপক আকারেই আছে।
পরিস্থিতি আরও প্রকট হয় এক দশক আগে, যখন স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার নেপাল দ্রুত বাড়তে থাকে। এমনকি কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূচকে তারা ভারতকেও পেছনে ফেলে দেয়। তখনো আগের মতোই এটিকে স্বল্পমেয়াদি অসংগতি বলে ঠাহর করা হয়; কিন্তু এই ‘স্বল্প মেয়াদ’ ভারত এখনো পার করতে পারেনি! নেপালের মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন যৎসামান্য হলেও এটি কীভাবে সম্ভব হলো, তা আমাদের ধন্দে ফেলতে পারে।
প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ও নেপালে আদতে কী ঘটছে, তা বুঝতে হলে এসব ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে অনুসন্ধান করলে সন্ধান মিলতে পারে। যেমন কম খরচে গণস্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে। ডায়রিয়া বা পানিশূন্যতা থেকে জীবন বাঁচাতে খাওয়ার স্যালাইনের বিপুল ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে অনেক বাহবা কুড়িয়েছে। এখানেই গল্পের শেষ নয়, বরং একটিমাত্র দিক। অথবা এমনও তো হতে পারে যে প্রকৃত রহস্য বাংলাদেশ বা নেপালÑদুই দেশের কোথাও নেই, বরং লুকিয়ে আছে খোদ ভারতেই।
এই কথায় সবার মনোযোগ যখন ভারতের দিকে ফিরবে, ঠিক তখনই প্রেক্ষাগৃহে চটজলদি এক অতিকায় হাতি ঢুকে পড়বে, সে আর কেউ নয়, দ্বৈত্যাকৃতির সামাজিক বৈষম্য। তবে ভারতে বৈষম্যের অভিনবত্ব হলো, এটি পরস্পর-নির্ভরশীল বহুস্তরীয় বৈষম্যের এক জটিল চোরাবালিতে সমাজকে আবদ্ধ করে রেখেছে, যার শিকড় বহুদিনের ক্ষতিকর ও নিষ্ঠুর বর্ণপ্রথার মধ্যে। অসাম্য যে কেবল ভারতেই আছে এমন নয়, বরং গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় তার মূল বেশ গভীরে বিস্তৃত। কিন্তু এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনায় ভারত শীর্ষে থাকবে। কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন, কেন দ্রুত আর্থিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতের সামাজিক উন্নয়নের গতি এতটা মন্থর? এই প্রশ্নের উত্তর জানলে ভারতের স্বরূপ অল্প হলেও বোঝা সম্ভব হতো।
অতিসম্প্রতি কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ ভারতে এখনো দূর না হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো দক্ষ পয়োবর্জ্য নিষ্কাশনব্যবস্থা গড়তে গোটা সমাজের সামষ্টিক-কর্তব্যবোধ কাজ করেনি। পয়োনিষ্কাশনের কাজটি সনাতনী ধারায় বর্ণপ্রথার সবচেয়ে নিচু বর্গের কাজ হিসেবে মনে করা হতো। একইভাবে ভারতীয় সমাজে নারীর ক্ষমতাহীনতা ও চরম অবদমনের কারণে শিশু-অপুষ্টি বেড়ে গেছে।
সামাজিক অসমতার সঙ্গে মানব উন্নয়নের আরও কিছু নেতিবাচক সম্পর্ক আছে। যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক সহযোগিতার ফলাফল হলো মানব উন্নয়ন। কিন্তু যখন একটি সমাজ শুধুই বিভক্তই নয়, বরং বহুস্তরীয় বৈষম্যে জর্জরিত, তখন সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলাই অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো, যেখানে মা–বাবা, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সবাই সমন্বিত হয়ে দেশের প্রত্যেক শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন, তাহলে পুরো ভারতের চিত্র কতই-না বদলে যেত!
প্রকৃত অর্থেই এটি ঘটলে ভারতের স্কুলগুলো আগাগোড়াই পাল্টে যেত। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব থাকার কারণে পুরো দেশটিই বদলে যেত এবং একই সঙ্গে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনও যেত বদলে। কিন্তু হায়! কল্পনা ও বাস্তব এক নয়; বাস্তবতা হলো, ভারতের স্কুলগুলোতে সহযোগিতার পরিবেশ একেবারেই প্রচলিত নয়। স্কুলের পাঠ্যসূচিসহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেন শুধু ফার্স্ট বয়দেরই খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাদের অগ্রগিতিতে সহযোগিতা করা যায়। কিন্তু এই বিজয়ীরা সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ, যারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত; বস্তুত কেবল তাদেরই দেশের অভিজাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব উচ্চবর্ণের হিন্দু শিক্ষকদের বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়। ‘গোদের উপর বিষফোড়া’র মতো এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সঙ্গে গরিব অভিভাবকের, বিশেষত মায়েদের সামাজিক দূরত্ব এতটাই যে এতে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে তাদের সমন্বয়ে একটি স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠন করাও বেশ কঠিন বিষয়। এ রকম বন্ধুর পথে মানসম্পন্ন সর্বজনীন শিক্ষার অগ্রগতি হবে খুব ধীর, এতে অবাক হওয়ার কী আছে।
ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাতী নারায়ণের গভীর ও যতœশীল কাজ এটি। মানব উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক অসমতার আন্তসম্পর্ক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে আনা হয়েছে এতে। একনিষ্ঠ অন্বেষণে প্রাপ্ত ফলাফল এই গ্রন্থে সবার জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। স্বাতীর কাজ একদিকে যেমন দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজকে অসমতার কতখানি খেসারত দিতে হচ্ছে তাতে আলো ফেলেছে, অন্যদিকে পরিবর্তনের সম্ভাবনার দিকটি দেখানো হয়েছে। কেরালা থেকে একদম নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন অগণিত আশাপ্রদ সাফল্য নিয়ে এসেছে, তাও দেখিয়েছেন তিনি।
মানব উন্নয়নের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা ও তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা মোটেও সহজ কাজ নয়। নিশ্চিতভাবেই ধাঁধাগুলোর কিছু অংশ আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে যাবে; বাদবাকি অংশ বোঝার জন্য আছে অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা শ্বাসরুদ্ধকর প্রকট বৈষম্য উপেক্ষা করা কঠিন। স্বাতী নারায়ণের বইটি এই মৌলিক সম্পর্ক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছে। পাঠক ‘কার্য-কারণ’ সম্পর্ক আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে বইটি পাঠ করলে তাঁদের ক্ষুধা হয়তো না–ও মিটতে পারে। এর বদলে আপনি যদি ভাবনার খোরাক খোঁজেন, তাহলে বইটি নির্দ্বিধায় আপনার জন্য।
ভারতীয় লেখক স্বাতী নারায়ণ রচিত ‘আনইকুয়াল’ বা ‘অসম’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে ভারতের কনটেক্সট প্রকাশনী (ওয়েস্টল্যান্ড বুকস) থেকে। সেই বইয়ের মুখবন্ধ লেখেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও অমর্ত্য সেনের সহলেখক জঁ দ্রেজ। লেখকের অনুমোদন সাপেক্ষে ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদ করা হলো।
জঁ দ্রেজ: বেলজিয়াম বংশোদ্ভূত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস ও দিল্লি স্কুল ইকোনমিকসে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।
অনুবাদ: আহমেদ জাভেদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন।